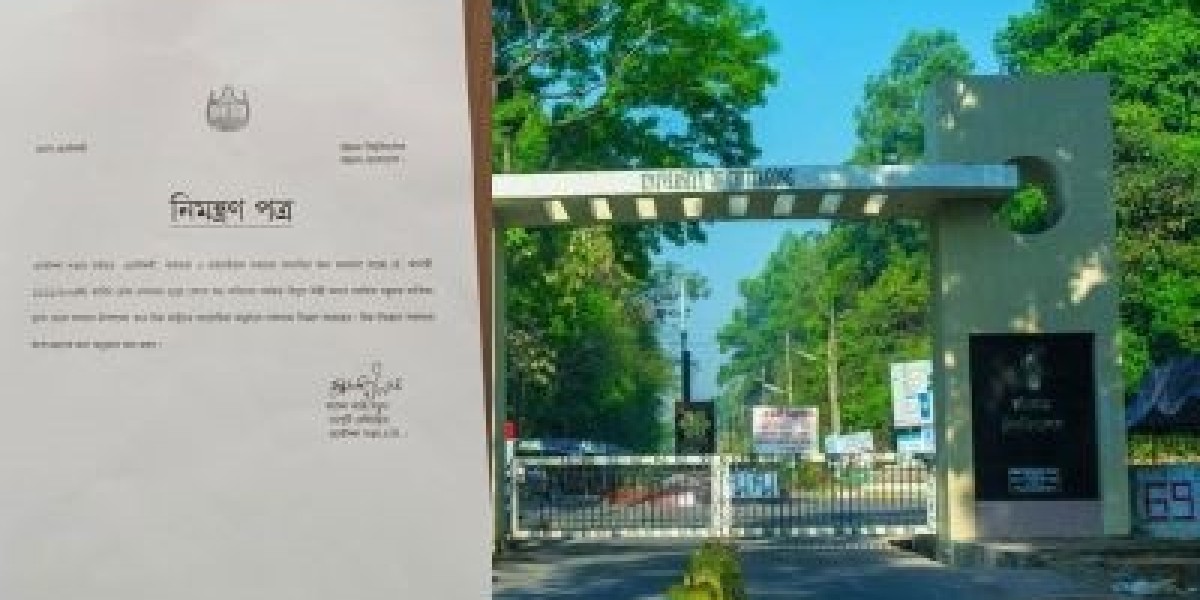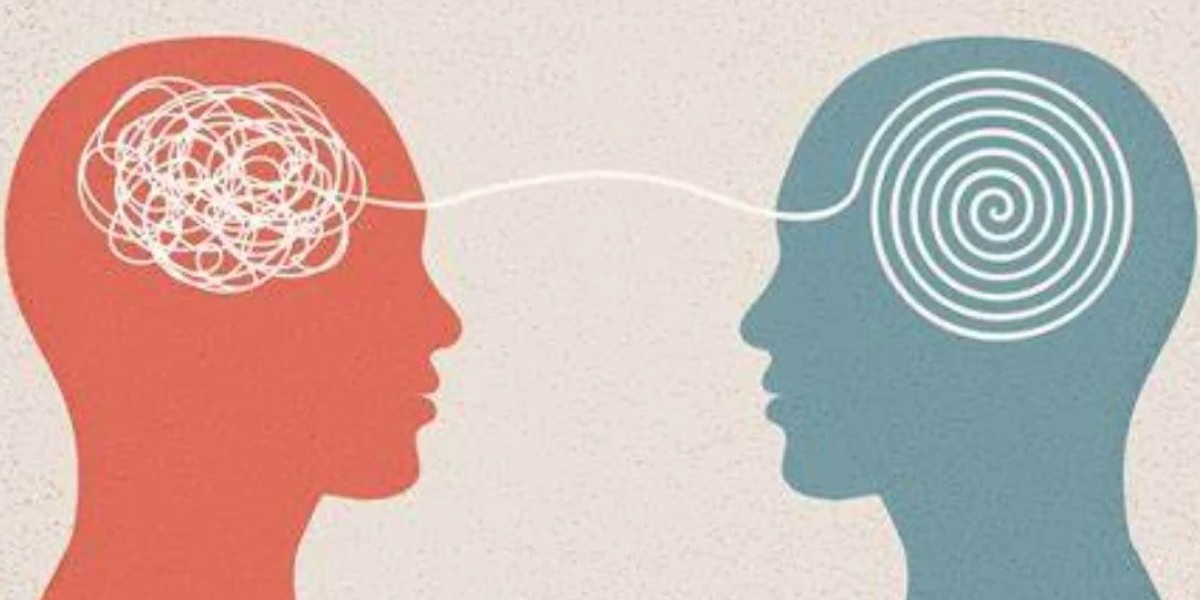এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, ইংরেজ কবি ড্রাইডেনের রচিত সংগীত-বিষয়ক একটি কবিতা বিনয় ভাবব্যক্তির সহিত আবৃত্তি করিয়া যাইবে এবং মেয়েরা অভিনয়মঞ্চে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইয়া কাব্যলিখিত ব্যাপারের মূক অভিনয় করিতে থাকিবে। এ ছাড়া মেয়েরাও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং গান প্রভৃতি করিবে।
বরদাসুন্দরী বিনয়কে অনেক ভরসা দিয়াছিলেন যে, তাহাকে তাঁহারা কোনোপ্রকারে তৈরি করিয়া লইবেন। তিনি নিজে ইংরেজি অতি সামান্যই শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দলের দুই-এক জন পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার নির্ভর ছিল।
কিন্তু যখন আখড়া বসিল, বিনয় তাহার আবৃত্তির দ্বারা বরদাসুন্দরীর পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিল। তাঁহাদের মণ্ডলীবহির্ভূত এই ব্যক্তিকে গড়িয়া লইবার সুখ হইতে বরদাসুন্দরী বঞ্চিত হইলেন। পূর্বে যাহারা বিনয়কে বিশেষ কেহ বলিয়া খাতির করে নাই তাহারা, বিনয় এমন ভালো ইংরেজি পড়ে বলিয়া তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন-কি, হারানবাবুও তাঁহার কাগজে মাঝে মাঝে লিখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। এবং সুধীর তাহাদের ছাত্রসভায় মাঝে মাঝে ইংরেজি বক্তৃতা করিবার জন্য বিনয়কে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।
ললিতার অবস্থাটা ভারি অদ্ভুত-রকম হইল। বিনয়কে যে কোনো সাহায্য কাহাকেও করিতে হইল না সেজন্য সে খুশিও হইল, আবার তাহাতে তাহার মনের মধ্যে একটা অসন্তোষও জন্মিল। বিনয় যে তাহাদের কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরঞ্চ তাহাদের সকলের চেয়ে ভালো, সে যে মনে মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনোপ্রকার শিক্ষার প্রত্যাশা করিবে না, ইহাতে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। বিনয়ের সম্বন্ধে সে যে কী চায়, কেমনটা হইলে তাহার মন বেশ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মাঝে হইতে তাহার অপ্রসন্নতা কেবলই ছোটোখাটো বিষয়ে তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়কেই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিনয়ের প্রতি ইহা যে সুবিচার নহে এবং শিষ্টতাও নহে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া সে কষ্ট পাইল এবং নিজেকে দমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু অকস্মাৎ অতি সামান্য উপলক্ষেই কেন যে তাহার একটা অসংগত অন্তর্জ্বালা সংযমের শাসন লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। পূর্বে যে ব্যাপারে যোগ দিবার জন্য সে বিনয়কে অবিশ্রাম উত্তেজিত করিয়াছে এখন তাহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু এখন সমস্ত আয়োজনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া বিনয় অকারণে পলাতক হইবে কী বলিয়া? সময়ও আর অধিক নাই; এবং নিজের একটা নূতন নৈপুণ্য আবিষ্কার করিয়া সে নিজেই এই কাজে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।
অবশেষে ললিতা বরদাসুন্দরীকে কহিল, “আমি এতে থাকব না।”
বরদাসুন্দরী তাঁহার মেজো মেয়েকে বেশ চিনিতেন, তাই নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”
ললিতা কহিল, “আমি যে পারি নে।”
বস্তুত যখন হইতে বিনয়কে আর আনাড়ি বলিয়া গণ্য করিবার উপায় ছিল না, তখন হইতেই ললিতা বিনয়ের সম্মুখে কোনোমতেই আবৃত্তি বা অভিনয় অভ্যাস করিতে চাহিত না। সে বলিত, “আমি আপনি আলাদা অভ্যাস করিব।’ ইহাতে সকলেরই অভ্যাসে বাধা পড়িত, কিন্তু ললিতাকে কিছুতেই পারা গেল না। অবশেষে, হার মানিয়া অভ্যাসক্ষেত্রে ললিতাকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।
কিন্তু যখন শেষ অবস্থায় ললিতা একেবারেই ভঙ্গ দিতে চাহিল তখন বরদাসুন্দরীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি জানিতেন যে তাঁহার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতেই পারিবে না। তখন তিনি পরেশবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। পরেশবাবু সামান্য বিষয়ে কখনোই তাঁহার মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই অনুসারে সে পক্ষও আয়োজন করিয়াছেন, সময়ও অত্যন্ত সংকীর্ণ, এই-সমস্ত বিবেচনা করিয়া পরেশবাবু ললিতাকে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, “ললিতা, এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অন্যায় হবে।”
ললিতা রুদ্ধরোদন কণ্ঠে কহিল, “বাবা, আমি যে পারি নে। আমার হয় না।”
পরেশ কহিলেন, “তুমি ভালো না পারলে তোমার অপরাধ হবে না, কিন্তু না করলে অন্যায় হবে।”
ললিতা মুখ নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; পরেশবাবু কহিলেন, “মা, যখন তুমি ভার নিয়েছ তখন তোমাকে তো সম্পন্ন করতেই হবে। পাছে অহংকারে ঘা লাগে বলে আর তো পালাবার সময় নেই। লাগুক-না ঘা, সেটাকে অগ্রাহ্য করেও তোমাকে কর্তব্য করতে হবে। পারবে না মা?”
ললিতা পিতার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, “পারব।”
সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ করিয়া বিনয়ের সম্মুখেই সমস্ত সংকোচ সম্পূর্ণ দূর করিয়া সে যেন একটা অতিরিক্ত বলের সঙ্গে, যেন স্পর্ধা করিয়া নিজের কর্তব্যে প্রবৃত্ত হইল। বিনয় এতদিন তাহার আবৃত্তি শোনে নাই। আজ শুনিয়া আশ্চর্য হইল। এমন সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ, কোথাও কিছুমাত্র জড়িমা নাই, এবং ভাব-প্রকাশের মধ্যে এমন একটা নিঃসংশয় বল যে, শুনিয়া বিনয় প্রত্যাশাতীত আনন্দ লাভ করিল। এই কণ্ঠস্বর তাহার কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল।
কবিতা-আবৃত্তিতে ভালো আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে। সেই কবিতার ভাবটি তাহার পাঠককে মহিমা দান করে– সেটা যেন তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার মুখশ্রী, তাহার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া দেখা দেয়। ফুল যেমন গাছের শাখায় তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে।
ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। যেখানে ব্যথা সেইখানেই কেবলই যেমন হাত পড়ে, বিনয়ও তেমনি কয়দিন ললিতার উষ্ণ বাক্য এবং তীক্ষ্ণ হাস্য ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারে নাই। কেন যে ললিতা এমন করিল, তেমন বলিল, ইহাই তাহাকে বারংবার আলোচনা করিতে হইয়াছে; ললিতার অসন্তোষের রহস্য যতই সে ভেদ করিতে না পারিয়াছে ততই ললিতার চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ ভোরের বেলা ঘুম হইতে জাগিয়া সে কথা তাহার মনে পড়িয়াছে, পরেশবাবুর বাড়িতে আসিবার সময় প্রত্যহই তাহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে আজ না জানি ললিতাকে কিরূপভাবে দেখা যাইবে। যেদিন ললিতা লেশমাত্র প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছে সেদিন বিনয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে এবং এই ভাবটি কী করিলে স্থায়ী হয় সেই চিন্তাই করিয়াছে, কিন্তু এমন কোনো উপায় খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার আয়ত্তাধীন।
এ কয়দিনের এই মানসিক আলোড়নের পর ললিতার কাব্য-আবৃত্তির মাধুর্য বিনয়কে বিশেষ করিয়া এবং প্রবল করিয়া বিচলিত করিল। তাহার এত ভালো লাগিল যে, কী বলিয়া প্রশংসা করিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার মুখের সামনে ভালোমন্দ কোনো কথাই বলিতে তাহার সাহস হয় না– কেননা তাহাকে ভালো বলিলেই যে সে খুশি হইবে, মনুষ্যচরিত্রের এই সাধারণ নিয়ম ললিতার সম্বন্ধে না খাটিতে পারে– এমন-কি, সাধারণ নিয়ম বলিয়াই হয়তো খাটিবে না– এই কারণে বিনয় উচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া বরদাসুন্দরীর নিকট ললিতার ক্ষমতার অজস্র প্রশংসা করিল। ইহাতে বিনয়ের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা আরো দৃঢ় হইল।
আর-একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। ললিতা যখনই নিজে অনুভব করিল তাহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে, সুগঠিত নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া যেমন করিয়া চলিয়া যায় সেও যখন তেমনি সুন্দর করিয়া তাহার কর্তব্যের দুরূহতার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তখন হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহার তীব্রতাও দূর হইল। বিনয়কে বিমুখ করিবার জন্য তাহার চেষ্টামাত্র রহিল না। এই কাজটাতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল এবং রিহার্সাল ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল। এমন-কি, আবৃত্তি অথবা অন্য কিছু সম্বন্ধে বিনয়ের কাছে উপদেশ লইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না।
ললিতার এই পরিবর্তনে বিনয়ের বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। এত আনন্দ হইল যে, যখন-তখন আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বালকের মতো ছেলেমানুষি করিতে লাগিল। সুচরিতার কাছে বসিয়া অনেক কথা বকিবার জন্য তাহার মনে কথা জমিতে থাকিল, কিন্তু আজকাল সুচরিতার সঙ্গে তাহার দেখাই হয় না। সুযোগ পাইলেই ললিতার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিত, কিন্তু ললিতার কাছে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইয়াই কথা বলিতে হইত; ললিতা যে মনে মনে তাহাকে এবং তাহার সকল কথাকে তীক্ষ্ণভাবে বিচার করে ইহা জানিত বলিয়া ললিতার সম্মুখে তাহার কথার স্রোতে স্বাভাবিক বেগ থাকিত না। ললিতা মাঝে মাঝে বলিত, “আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বলছেন, এমন করে বলেন কেন?”
বিনয় উত্তর করিত, “আমি যে এত বয়স পর্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেইজন্য মনটা ছাপার বইয়ের মতো হয়ে গেছে।”
ললিতা বলিত, “আপনি খুব ভালো করে বলবার চেষ্টা করবেন না– নিজের কথাটা ঠিক করে বলে যাবেন। আপনি এমন চমৎকার করে বলেন যে, আমার সন্দেহ হয় আপনি আর-কারো কথা ভেবে সাজিয়ে বলছেন।”
এই কারণে, স্বাভাবিক ক্ষমতাবশত একটা কথা বেশ সুসজ্জিত হইয়া বিনয়ের মনে আসিলে ললিতাকে বলিবার চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহা সাদা করিয়া এবং স্বল্প করিয়া বলিতে হইত। কোনো একটা অলংকৃত বাক্য তাহার মুখে হঠাৎ আসিলে সে লজ্জিত হইয়া পড়িত।
ললিতার মনের ভিতর হইতে একটা যেন অকারণ মেঘ কাটিয়া গিয়া তাহার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বরদাসুন্দরীও তাহার পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে এখন পূর্বের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসে না, সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। আগামী অভিনয়ের সাজসজ্জা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহার মনে প্রত্যহ নানাপ্রকার নূতন নূতন কল্পনার উদয় হইতে লাগিল, তাহাই লইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর উৎসাহ যতই বেশি হউক তিনি খরচের কথাটাও ভাবেন– সেইজন্য, ললিতা যখন অভিনয়-ব্যাপারে বিমুখ ছিল তখনো যেমন তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ ঘটিয়াছিল এখন তাহার উৎসাহিত অবস্থাতেও তেমনি তাঁহার সংকট উপস্থিত হইল। কিন্তু ললিতার উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তিকে আঘাত করিতেও সাহস হয় না, যে কাজে সে উৎসাহ বোধ করে সে কাজের কোথাও লেশমাত্র অসম্পূর্ণতা ঘটিলে সে একেবারে দমিয়া যায়, তাহাতে যোগ দেওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।
ললিতা তাহার মনের এই উচ্ছ্বসিত অবস্থায় সুচরিতার কাছে অনেকবার ব্যগ্র হইয়া গিয়াছে। সুচরিতা হাসিয়াছে, কথা কহিয়াছে বটে, কিন্তু ললিতা তাহার মধ্যে বারংবার এমন একটা বাধা অনুভব করিয়াছে যে, সে মনে মনে রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।
একদিন সে পরেশবাবুর কাছে গিয়া কহিল, “বাবা, সুচিদিদি যে কোণে বসে বসে বই পড়বে, আর আমরা অভিনয় করতে যাব, সে হবে না। ওকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।”
পরেশবাবুও কয়দিন ভাবিতেছিলেন, সুচরিতা তাহার সঙ্গিনীদের নিকট হইতে কেমন যেন দূরবর্তিনী হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থা তাহার চরিত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন। ললিতার কথা শুনিয়া আজ তাহার মনে হইল, আমোদপ্রমোদে সকলের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে সুচরিতার এইরূপ পার্থক্যের ভাব প্রশ্রয় পাইয়া উঠিবে। পরেশবাবু ললিতাকে কহিলেন, “তোমার মাকে বলো গে।”
ললিতা কহিল, “মাকে আমি বলব, কিন্তু সুচিদিদিকে রাজি করাবার ভার তোমাকে নিতে হবে।”
পরেশবাবু যখন বলিলেন তখন সুচরিতা আর আপত্তি করিতে পারিল না– সে আপন কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইল।